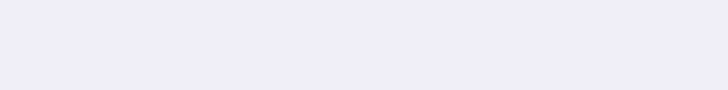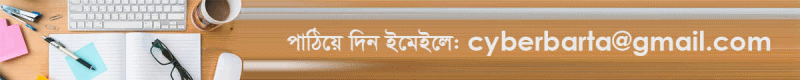সাইবারবার্তা ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক টাইমসের এই পোস্টে দেখানো হয়েছে: কিভাবে ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে, একজন উচ্চশিক্ষিত নারীর ফেসবুক পোস্ট নাটকীয়ভাবে ঝুঁকে পড়েছে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের দিকে।
ভ্যালেরি গিলবার্ট হার্ভার্ড-পড়ুয়া একজন উচ্চশিক্ষিত নিউইয়র্কবাসী; এবং স্বঘোষিত “মিম রানি”। কিউঅ্যানন যোদ্ধা হিসেবে গিলবার্ট তথ্য ছড়ান অনেক বিস্তৃত পরিসরে। যেমন: “শয়তানের অনুসারী শিশু যৌন নিপীড়কদের” একটি বৈশ্বিক গুপ্ত চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই নাকি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ক্ষমতায় এনেছিল শীর্ষস্থানীয় সেনা কর্মকর্তারা। অবশ্যই, এসব বার্তা প্রচারের জন্য গিলবার্টের পছন্দের মাধ্যম: ভার্চ্যুয়াল জগতের ক্ষণস্থায়ী বিনোদন, ইন্টারনেট মিম।
গিলবার্ট কীভাবে দিনে দিনে এমন উগ্রপন্থী হয়ে উঠলেন, সেটিই খতিয়ে দেখেছেন নিউইয়র্ক টাইমসের রেভিন রুজ। এ জন্য তিনি বিশ্লেষণ করেছেন গিলবার্টের শেয়ার করা সব মিম। প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও সংস্কৃতির সংযোগ নিয়ে পত্রিকাটিতে “দ্য শিফট” নামের একটি কলাম লেখেন রুজ। “আ কিউঅ্যানন “ডিজিটাল সোলজার” মার্চেস অন, আনডেটার্ড বাই থিওরি’স আনর্যাভেলিং” শিরোনামের এই কলামে রুজ ব্যবহার করেছেন প্রথাগত রিপোর্টিং পদ্ধতি, গিলবার্টের নিজের কণ্ঠ ও ফেসবুক পেজ থেকে তুলে আনা মিমগুলোর ভিজ্যুয়াল উপস্থাপন। এই সবকিছু মিলিয়ে দেখানো হয়েছে: কীভাবে একজন হতাশ হয়ে পড়া, অভিজাত লেখক ও অভিনেত্রী উগ্রপন্থী হয়ে উঠছেন অনলাইনে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের পথে পা দিয়ে, যেগুলো তিনি পাচ্ছেন ছদ্ম-বাম থেকে শুরু করে পুরোদস্তুর কিউঅ্যানন গ্রুপগুলোর কাছ থেকে।
সামাজিক-রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে এখন খুবই কার্যকর উপাদান হিসেবে কাজ করে মিম। এতে লুকানো অর্থ এবং অনেক ধরনের তথ্য খুবই অল্প জায়গার মধ্যে বলে দেওয়া যায়। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইন্টারনেটের যুগে উগ্রপন্থী যোদ্ধাদের অস্ত্রভান্ডারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হলো মিম। তবে, রুজের অনুসন্ধানে যথাযথভাবে উঠে এসেছে: ঠিক কীভাবে ব্যাপারটি ঘটে এবং কত বিচিত্র রকমের মানুষ এ ধরনের যোগাযোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। কীভাবে এই প্রতিবেদন করা হলো, তা জানতে রুজের সঙ্গে কথা বলেছে স্টোরিবেঞ্চ। (দৈর্ঘ্য ও স্পষ্টতার কথা বিবেচনা করে সাক্ষাৎকারটি সম্পাদনা করা হয়েছে।)
এসবি: কীভাবে লেখাটি শুরুর পরিকল্পনা করলেন? অনুপ্রেরণা কী ছিল? ভ্যালেরি গিলবার্টকে কীভাবে খুঁজে পেলেন?
কেআর: ভ্যালেরিকে খুঁজে পাই সম্ভবত ২০১৯ সালের দিকে। আমি সে সময় একটি পডকাস্ট তৈরি করছিলাম এবং সত্যিই এমন কাউকে খুঁজছিলাম, যিনি কিউঅ্যাননে বিশ্বাস করেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলবেন। যত দূর মনে পড়ে, আমার এক প্রযোজক তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন টুইটারে। তিনি কিউঅ্যানন নিয়ে টুইট করছিলেন এবং নিউইয়র্কে থাকেন। আমরা খুবই খুশি হই; কারণ, তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলা যাবে। আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তিনি কথা বলতেও রাজি হন। এরপর তিনি আসেন এবং আমি তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিই। কিন্তু পডকাস্টটি আর আমাদের বানানো হয়নি। আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। কয়েক মাস আগেও তাঁর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “কেমন চলছে দিনকাল? নতুন কিছু করছেন?” আমার মনে হয়েছিল, তাঁর গল্পটি সবাইকে বলা দরকার। ছাঁচেঢালা একটি ধারণা আছে যে, কিউঅ্যাননে বিশ্বাসীরা নির্বোধ বা অশিক্ষিত ধরনের হয় এবং তারা অপরিশীলিত সব জায়গা থেকে সংবাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি দেখাতে চেয়েছি, এটি অনেক ক্ষেত্রে সত্য নয়। উচ্চশিক্ষা, অবস্থান এবং অনেক সম্পদ থাকার পরও অনেকে এই ধরনের কমিউনিটির সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারেন।
কিউঅ্যানন ও ইন্টারনেটের এই জগৎ নিয়ে লেখালেখি শুরু করলেন কীভাবে?
আমি ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কাজ করি, এবং …ক্রাইস্টচার্চে গোলাগুলিটা আমার জন্য একটি বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। এরপর থেকে আমি আরও তলিয়ে দেখতে শুরু করি, কোনো ব্যক্তি কেন অনলাইনে উগ্র ও চরমপন্থী অবস্থান নিচ্ছে। এই ঘটনা সত্যিই আমার ওপর প্রভাব ফেলেছিল; অনলাইন উগ্রপন্থা যে অফলাইন উগ্রপন্থা থেকে ভিন্ন কিছু নয়, এর গুরুত্বও যে কোনো অংশে কম নয়, এবং প্রায়ই যে একটি থেকে অন্যটিতে রূপান্তর ঘটে, এই ঘটনা তার একটি নিদর্শন হয়ে উঠেছিল। এ রকম কিছু বিষয় চিন্তা করেই আমার মনে হয়েছে, বিষয়টি ভালো করে খতিয়ে দেখা উচিত।
আপনার এই প্রতিবেদনের ভিজুয়্যাল উপাদানগুলো ছিল সত্যিই নজরকাড়ার মতো। আমরা দেখতে পাই, কীভাবে গিলবার্টের পোস্টগুলো জিল স্টেইন ও শাকাহারের ধারা থেকে চরম ডানপন্থী পরিসরে চলে গেল। এই ভিজ্যুয়াল উপাদানগুলো কীভাবে এক জায়গায় করেছেন?

২০১৬ সালের দিকে, ভ্যালেরি গিলবার্ট এমন সব মিম শেয়ার করছিলেন, যেগুলো ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে যায়। ছবি: স্ক্রিনশট
কীভাবে কিউঅ্যাননের সঙ্গে যুক্ত হলেন, তা গিলবার্টের নিজের মুখ থেকে শোনা এক ব্যাপার। কিন্তুসেই জিনিসটি চোখের সামনে দেখবেন, আপনার চোখ খুলে যাবে। তার ফেসবুক পেজটিই আসলে গল্পগুলো বলছিল, যখন যা ঘটেছে- সেভাবেই। আপনি দেখতে পাবেন, কীভাবে তিনি একজন ডেমোক্র্যাট থেকে জিল স্টেইনের ভোটারে পরিণত হলেন। ডেমোক্র্যাটদের প্রতি মোহভঙ্গের পর তিনি কাউন্টার-কালচারাল ও ‘হ্যাকটিভিস্ট’ ধরনের (যেমন, জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ও এডওয়ার্ড স্নোডেন) ব্যক্তিত্বের প্রতি ঝুঁকে পড়তে থাকেন। এবং তিনি সত্যিই খুব সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন স্ট্যান্ডিং রক আন্দোলনের সঙ্গে। আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে, কীভাবে তাঁর এই বিশ্ব-দর্শন গড়ে উঠছে। আমার কাছে ব্যাপারটি খুবই মজার মনে হয়েছিল। আমি আমাদের গ্রাফিকস দলকে সঙ্গে নিয়ে কিছু বাছাই করা ফেসবুক পোস্ট তুলে আনি এবং দেখি যে, কীভাবে তাঁর চিন্তাভাবনা এগিয়েছে। মনে হয়েছিল, এভাবে আমরা অন্য মানুষদের সঙ্গেও একটি সংযুক্তি তৈরি করতে পারব। কেউ হয়তো এগুলো দেখে বলবে, “ও, আমি একজনকে চিনি, যে এ ধরনের মিম পোস্ট করে,” বা “আমি একজনের কথা জানি, যে এই একই ধরনের চিন্তাভাবনার মধ্যে আছে।” আমার মনে হতে থাকে, এটি একটি কাঠামো, যার সঙ্গে আমাদের সবারই কমবেশি পরিচয় আছে। এবং এটিই এই প্রতিবেদনটিতে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে।
মিমগুলো কীভাবে এই উগ্রপন্থী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে? এবং অন্যান্য টেক্সটভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যম থেকে এটি কীভাবে আলাদা?
মিম এখন রাজনৈতিক যোগাযোগ ও কৌশলের সবচেয়ে প্রথম সারির উপাদান হয়ে উঠেছে। এবং আমরা দেখছি যে, রাজনীতিবিদেরা এগুলো সাদরে গ্রহণ করছেন। মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পথে চিন্তা করানো এবং কথা বলানোর ক্ষেত্রে এটি হয়ে উঠছে একটি শর্টকাট। তবে মিম শুধু রাজনীতির বিষয় নয়, এটি এমন কিছুও নয়, যা শুধু চরমপন্থীরাই ব্যবহার করে। মিম ছড়িয়ে আছে সর্বত্র; এবং আমার মনে হয়, এ বিষয়টি হয়তো অন্যদের চেয়ে উগ্রপন্থীরাই আগে উপলব্ধি করেছিল যে, চরমপন্থার কার্যকর কৌশল তৈরির ক্ষেত্রে একটি বড় উপাদান হতে পারে মিম। যদি আপনার সবচেয়ে উগ্রপন্থী বিশ্বাসগুলো মিম ও হাস্যরসের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন; আপনি যদি শুধু ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের মতো আচরণ না করে, হাস্যরসাত্মক অনলাইন নিও-নাজি আকারে হাজির হতে পারেন, তাহলে আপনি সেসব মানুষের কাছেও আরও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবেন, যাঁরা সাধারণ সময়ে হয়তো আপনার আচরণ খুব একটা পছন্দ করতেন না। এটি হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট দর্শনের সঙ্গে মানুষকে এমনভাবে সংযুক্ত করার পদ্ধতি, যেখানে সিরিয়াস না হলেও চলে। এভাবে আপনি নারীবাদ বা “গ্রেট রিপ্লেসমেন্ট” বা অন্য কিছু নিয়ে একটু মজাও করে নিতে পারেন। আপনি যদি বিষয়গুলো হাস্যরসের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে হয়তো ভিন্নমত পোষণকারীদের রাগিয়ে দেওয়ার আশঙ্কাও কমিয়ে ফেলতে পারবেন। উগ্রপন্থী কৌশলের এই জাল খুব বিস্তৃতভাবে পাতা হয়েছে: মানুষ কখনোই নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না যে, কখন আপনি কথাটি গুরুত্ব দিয়ে বলছেন, আর কখন নয়।

২০২১ সাল নাগাদ ভ্যালেরি গিলবার্টের টুইটগুলোতে নাটকীয় পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস। ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল দাঙ্গার পর থেকে তিনি কিউঅ্যানন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট পোস্টের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। ছবি: স্ক্রিনশট
আমার মনে হয়, কিউঅ্যানন নিজে মৃত্যুদশায় পড়বে। সরকারের ভেতর থেকে কেউ একজন সরকারি তদন্ত এবং এ ধরনের তথ্য ফাঁস করছে- এ ধরনের ধ্যানধারণা আর বিশ্বাসযোগ্য থাকছে না। কারণ, ট্রাম্প এখন আর প্রেসিডেন্ট নন। আমার মতে, এটি এই আন্দোলন থেকে অনেক শক্তি সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কিউঅ্যাননে বিশ্বাস করা মানুষগুলো আবার সংবাদপত্র পড়ায় বা সংবাদ দেখায় ফিরে যাবে এবং মূলধারার কনজারভেটিভ বা লিবারালদের মতো আচরণ করা শুরু করবে। আমার মনে হয়, তারা আবার অন্য কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও অভিজাতদের অনিয়মসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের খোঁজ করবে। তারা হয়তো আর কিউ-এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে না, কিন্তু কিউঅ্যাননের মধ্য থেকে হয়তো অন্য কোনো ধরনের আন্দোলন দানা বাঁধবে। মিম ও ইন্টারনেট সংস্কৃতি, এখানে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। কারণ, এই কমিউনিটিগুলোর অন্যতম নীতি হলো: মূলধারার মিডিয়ার ছাঁকনির মধ্য দিয়ে আসা খবরগুলো অন্ধভাবে বিশ্বাস করা যাবে না। নিজে নিজে গবেষণা করে দেখতে হবে। ফলে এসবের অনেক কিছুই হয় নান্দনিক।
কিউঅ্যাননে বিশ্বাস করা কোনো মানুষ সন্ধ্যার সংবাদে বলা কথার চেয়ে, তার বন্ধুর পোস্ট করা কোনো মজার মিমের ওপর বেশি বিশ্বাস করবে। এটি প্রায় এমন এক তথ্য সরবরাহব্যবস্থা, যেখানে কোনো কিছুকে যত খারাপ মনে হবে, যত অমার্জিত মনে হবে, ততই সেটিকে বেশি সত্য মনে হবে। কারণ, এগুলো আসছে বিকল্প এক জগতের গবেষক ও অনুসন্ধানকারীদের কাছ থেকে, যাঁরা ইন্টারনেটে ছড়ানো বিভিন্ন ধরনের গুজব, পুরোনো স্ক্রিনশট ও উইকিপিডিয়া পেজের তথ্য দিয়ে একটা কিছু দাঁড় করাচ্ছেন। তাঁদের মনে হচ্ছে, তাঁরা এই নিষিদ্ধ জ্ঞানগুলো খুঁজে পেয়েছেন, এবং এগুলো কোনো কোট পরা মানুষের খবরে বলা তথ্যের চেয়ে অনেক বেশি সত্যি।
আপনার কি মনে হয়, গিলবার্টের মতো আরও অনেক উচ্চশিক্ষিত, অবস্থাসম্পন্ন মানুষও এমন তথ্য ছড়াচ্ছে এবং এ ধরনের কমিউনিটির সদস্য?

৭ জানুয়ারির এই পোস্টে, ভ্যালেরি গিলবার্ট এই ছবিটি শেয়ার করেছিলেন যেখানে দেখা যাচ্ছে ট্রাম্প সমর্থকরা ক্যাপিটলে হামলা চালিয়েছেন। কিন্তু ভ্যালেরি দাবি করছেন এরা আসলে “ছদ্মবেশে অ্যান্টিফা”। ছবি: স্ক্রিনশট
এমন ঠিক কতজন আছেন, নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল; কিন্তু আমি এমন কয়েকজন কিউঅ্যাননে বিশ্বাসী মানুষ পেয়েছি, যাঁদের শিক্ষাদীক্ষা আমার চেয়ে বেশি। তাঁদের বেশি ডিগ্রি আছে আমার চেয়ে। কয়েক সপ্তাহ আগে দ্য অ্যাটলান্টিকে মজার ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে তাঁরা ক্যাপিটল দাঙ্গায় গ্রেপ্তার হওয়া মানুষদের ডেটা বিশ্লেষণ করছিলেন। এতে দেখা যায়: আমরা যে ধরনের বাঁধাধরা চিন্তা করি, যেমন- অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে ক্ষুব্ধ তরুণেরা অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য বা অন্য যেকোনো কারণে এ ধরনের উগ্রপন্থায় ঝুঁকছে; ঘটনা মোটেও এমন নয়। সেখানে প্রধান নির্বাহী, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিক- এ ধরনের পয়সাওয়ালা, উচ্চশিক্ষিত মানুষ আছেন। ফলে আমার মনে হয়, এটি ধরে নেওয়া খুব ভুল হবে যে, এগুলোর সঙ্গে শুধু কম পড়াশোনা করা লাল অঙ্গরাজ্যের (রিপাবলিকানদের ভোটে জেতা রাজ্য) মানুষেরাই যুক্ত হন।
এই লেখার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?
এটি সত্যিই খুব মজার ছিল। আমি এমন অনেক মানুষের কাছ থেকে শুনেছি যে, “আমার মায়ের সঙ্গেও এমন হয়েছিল”। বা “আমার ভাইয়ের সঙ্গে এমন হয়েছে”, কিংবা “আমার প্রতিবেশীর সঙ্গে হয়েছে”। আমার মনে হয়, এত দিনে কিউঅ্যানন এবং অন্য ষড়যন্ত্র তত্ত্বের কমিউনিটিগুলো এতটাই বড় হয়ে উঠেছে যে, বেশির ভাগ মানুষই কাউকে না কাউকে দেখেছেন এই রাস্তায় চলে যেতে। ফলে এ নিয়ে অনেক হতাশা ও বিষণ্নতা আছে। কিন্তু এমন অনেক মানুষও আছেন, যাঁরা এই সমস্যার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন। তাঁরা জানতে চান: কীভাবে আমি কাউকে সেই বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরিয়ে আনব? কীভাবে তাঁদের সঙ্গে কথা বলব? কীভাবে তাঁদের বোঝাব, যেন তাঁরা কিউঅ্যাননের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত না হয়ে যায়? ফলে, আমার মনে হয়, অনেক মানুষ এই সমস্যার সমাধানও খুঁজছেন।লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব জার্নালিজমের স্টোরিবেঞ্চ-এ। অনুমতি নিয়ে এখানে পুনঃপ্রকাশ করা হলো। সৌজন্যে: জিআইজেএন
(সাইবারবার্তা.কম/আইআই/১ জুন ২০২১)